নামে আকারে গল্পে বিস্ময়ের অপর নাম হংসেশ্বরী মন্দির চিকিৎসক, লেখক ও ক্ষেত্র সমীক্ষক
প্রায় ২০০ বছর আগে বাংলার এক অজ গ্রামের স্কাইলাইন হঠাৎ বদলে গেল।
মাথা তুলল ৭০ ফুট উঁচু এক মন্দির, যার জুড়ি সারা বাংলা ঢুঁড়ে ফেললেও মিলবে না।
অথচ তাজ্জব ব্যাপার! মিল আছে ৫০০০ কিলোমিটার দূরের মস্কো শহরের সেন্ট বেসিল গির্জার সঙ্গে।
হংসেশ্বরী মন্দির।
জায়গার নাম? বাঁশবেড়িয়া।
যে নামকে ভেঙে বললে, বলতে হয় বাঁশের বেড়া!
তা ‘বেড়া’ র গল্প আছে বই কী!
পুঁথিপত্তর ঘেঁটে বেড়া-বৃত্তান্ত জানাও গিয়েছে খানিক।
এক সময় এ অঞ্চল ছিল দুর্ভেদ্য বাঁশ বন দিয়ে ঘেরা।
এদিকে জমিদারের নতুন কাছারি হবে।
তাই ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ সাফ হল বাঁশঝাড়।
বাঁশ কেটে ‘বাটী’, অর্থাৎ কিনা বাড়ি, তাই জায়গার নাম হল বংশবাটী।
তাই-ই লোকের মুখ ফিরতি হয়ে বাঁশবেড়ে। তারপর বাঁশবেড়িয়া।
গোড়ায় যে মন্দিরের কথা বললাম, সেটি তৈরি এক জমিদার-তনয়ের। জমিদার গোবিন্দদেব রায়ের পুত্র নৃসিংহদেব। এক সময় তিনি বিষয় মোহ ত্যাগ করে তন্ত্রসাধক হন। ১৭৯৯-এ তিনিই এখানে ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের মায়ের নামে যার নাম দেন হংসেশ্বরী মন্দির।
অনন্য এই মন্দিরের স্থাপত্য ভাবনা। একেবারে তন্ত্রভাবনা সঞ্জাত, যাকে বলে।
মন্দির তৈরির দো’তলা অবধি দেখে যেতে পেরেছিলেন নৃসিংহদেব।
তারপর হঠাৎই তাঁর দেহাবসান হয়।
তখন ছোট রানী শঙ্করী শেষ করেন স্বামীর আরব্ধ কাজ।
নির্মাণ-কার্য শেষ হয় ১৮১৪ সালে।
অর্থাৎ কিনা, আজ থেকে ২০০ বছরেরও আগে।
 |
| হংসেশ্বরী মাতা |
হাওড়া-কাটোয়া লোকাল বাঁশবেড়িয়ায় যখন পৌঁছে দিল তখন বেলা প্রায় এগারোটা।
‘‘মন্দির যাবেন তো? বসে পড়ুন।’’ টোটোওলার সহাস্য আশ্বাস।
দশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম।
ঢোকার মুখেই নহবতখানা। নীরব।
কতকাল? চুন সুরকির পলেস্তরা ওঠা ইট বের হওয়া থামগুলো জবাব জানে। এগোলাম। ডালা সাজিয়ে দোকানিরা।
জুতো রাখার জায়গা।
মন্দির।
সাত তলা উঁচু তো হবেই।
বিস্ময়!
তবে তা উচ্চতার জন্য নয়। দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো মিনারের মাথায় আধফোটা পদ্মের মতো সব চূড়া।
বিষণ্ণতা!
পাথরের তৈরি ১৩টি চূড়া ফ্যাকাশে স্বপ্নের মতো তাকিয়ে। আকাশপানে।
দেখলেই বোঝা যায়, বহুদিন রঙের পোঁচ পড়েনি মন্দিরে।
অনাদরের অভিমান তার সর্বাঙ্গে। তবু সে এখনও সমীহ আদায় করে ছাড়ে।
আর এক পলক সময় গড়ালেই প্রশ্ন উঁকি মারে মনে, ২০০ বছর আগের গ্রামবাংলায় কেমন করে হাজির হল এই বেনজির স্থাপত্যরীতি!
চলে যাই তারই গল্পে।
অনেকের মতে, এই মন্দির হচ্ছে তান্ত্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। যদিও স্থাপত্যরীতির মধ্যে তান্ত্রিক-স্থাপত্য বলে কোন কিছু হয় না। তান্ত্রিক মত হচ্ছে এক প্রচলিত ধর্মপালনের রীতিনীতি। যা হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মে প্রচলিত আছে।
তান্ত্রিক মতে, দেহের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদি ৫টি নাড়ী আছে, সুষুম্নাকান্ডকে কেন্দ্র করে। এই সুষুম্নাকান্ড বরাবর বিভিন্ন স্থানে ৬টি চক্র রয়েছে।
এই চক্রগুলির একদম নীচের চক্রটির নাম মূলাধার চক্র, যেখানে রয়েছে সর্পাকৃতি ‘কুলকুণ্ডলিনী’। তান্ত্রিক নৃসিংহদেব মানবদেহের এই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বকেই মন্দিরের স্থাপত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। |
| হংসেশ্বরী মন্দিরে অপরূপ কাঠের মহিষাসুরমর্দিনী |
মন্দিরের গর্ভগৃহে অর্থাৎ ‘মূলাধারে’ সহস্রদল পদ্মের উপরে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপ দেবী হংসেশ্বরী বিরাজমান। মন্দিরে বিভিন্ন স্থান দিয়ে পাঁচটি প্রধান নাড়ীর রূপক হিসাবে পাঁচটি সিঁড়ি উঠে গিয়েছে।
এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলে রয়েছে একটি বিচিত্র গোলকধাঁধা। যার মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে পথপ্রদর্শকের সাহায্য ছাড়া সহজে বার হয়ে আসা মুশকিল।
এও এক ভুলভুলাইয়া!
এই গোলকধাঁধারই একস্থানে একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিরাজ করছেন শ্বেতপাথরের সদাশিব। এর অর্থ হল, প্রকৃত গুরুর দেখানো পথ ধরেই মূলাধারের শক্তিকে নাড়ীর মাধ্যমে চালিত করে হৃদিপদ্মে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত করা সম্ভব।
এরই তান্ত্রিক পরিভাষার যার নাম ‘ষটচক্রভেদ’।
আবার ভিন্ন মতও কি নেই?
সেই কথায় যাই।
হুগলি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পর্তুগিজ প্রভাব ছিল। ত্রিবেণী বা সম্ভবত বাঁশবেড়িয়াতে তাদের বসতি স্থাপন হয় ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে, সম্রাট আকবরের দেওয়া ফরমান অনুসারে।
পেড্রো ট্যাভার্স নামক একজন পর্তুগিজ ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে খুশি হয়ে আকবর এই ফরমান জারি করেছিলেন। সম্রাটের জীবনীকার আবুল ফজলের বর্ণনা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, আকবরের জমানায় সাতগাঁও এবং হুগলি নদী বন্দর পর্তুগীজদের অধীনে ছিল। কিন্তু আকবরের ফরমানের অপব্যবহার করে পর্তুগীজরা লুটপাট, ডাকাতি আর দাস-ব্যবসা শুরু করল, এমনকী এক সময় তাঁরা মুঘলদের রাজস্ব দেওয়াও বন্ধ করে দিলে। তখন শাহজাহানের নির্দেশে তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁ পর্তুগীজদের বাড়ি ঘর, গির্জা, দুর্গ সব ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দেন।
তখন শাহজাহানকে খুশি করে ব্যবসার সনদ বা ফরমান নিয়ে প্রথমে ১৬২৫ সালে ওলন্দাজরা আসে চুঁচুড়ায়।
১৬৩৮ সালে ইংরেজরা আসে হুগলি বন্দর অঞ্চলে ব্যবসা করতে।
ফরাসিরা চন্দননগরে আসে ১৬৭৪ সালে।
ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে আসে দিনেমাররা। প্রতিষ্ঠা করে দিনেমার ডাঙ্গা।
এভাবেই আরও জুটেছিল বেলজিয়ান, জার্মান, গ্রীক ও আর্মেনিয়ানরা।
এই ধরনের অদ্ভুত কিন্তু অসাধারণ সুন্দর স্থাপত্য নির্মাণে সম্ভবত সেই সময়ের মিশ্র পাশ্চাত্য স্থাপত্যধারার অনুপ্রেরণা রয়েছে। |
| হংসেশ্বরী মন্দিরে পার্বতী পুত্র |
একই মন্দির।
অথচ তার নির্মাণের পিছনে কত গল্প গাথা!
গোল বেদির উপরে নিম কাঠে নির্মিত, নীলবর্ণা, ত্রিনয়নী, চতুর্ভূজা, নরমুন্ডশোভিতা হংসেশ্বরী দেবী মূর্তি মহাদেবের নাভিপদ্মের উপর দন্ডায়মান।
বিগ্রহের বর্ণ নীল। মাথায় ঘোমটা।
সারাবছর সেই রূপ শান্ত রূপ।
তবে কার্তিক মাসের কালীপুজোয় একরাতের জন্য রূপ হয় এলোকেশী!
রীতি। পরম্পরা। তাই।
দেখা শেষ।
ফেরার পালা।
মন যদিও উল্টোপথে হাঁটছে। ভাবছিলাম কেমন ছিল আশপাশটা ২০০ বছর আগে? কত গড়াভাঙ্গার খেলাই না দেখেছে এই মন্দির তার জন্মকাল থেকে! সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে?
‘‘স্টেশন যাবেন তো?’’
চমক ভাঙল একটা ডাকে।
ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেই ছেলেটি! হাসিমুখ।
টোটো কোম্পানি!
বললাম, ‘‘চল।’’
ছবিঃ প্রতিবেদক
সম্পাদনা সহযোগীঃ কৌশিক দাশগুপ্ত
 |
| হংসেশ্বরী মন্দির | |
আমাদের ব্লগে প্রকাশিত আরও লেখা











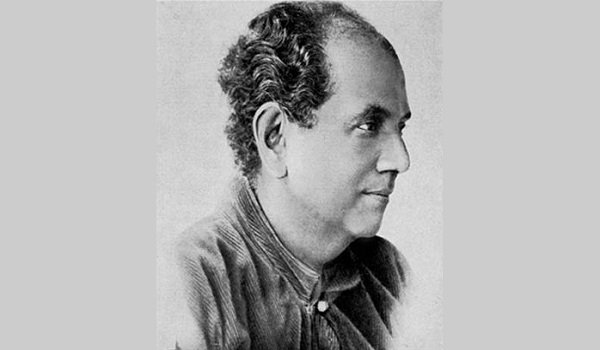

No comments:
Post a Comment