চতুর্ভূজা দুর্গা ও প্রাচীন গাঁ পিয়াসাড়ার গল্প অনেকটা যেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ২য় পর্ব শিক্ষক, আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চাকারী
পাশাপাশি আরেকটি কাণ্ড ঘটল।
এদিকে ততদিনে তারকেশ্বরে বনের মধ্যে শিবশিলা আত্মপ্রকাশ করেছেন।
তারকেশ্বরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে দশনামী সন্ন্যাসীদের মঠ।
তারকেশ্বরের মঠের বিপুল সম্পত্তি নানা কারণে বেদখল হয়ে যেতে থাকছে। তখন মোহান্ত রঘুচন্দ্র গিরি তাঁর বিপুল সম্পত্তি দেখাশোনার ভার জমিদার আনন্দমোহন সরকারের হাতে দিলেন। এই আনন্দমোহন মানুষটি হলেন ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র।[৩]
বর্ধমান রাজের তারকেশ্বর পৃষ্ঠপোষকতার কথা সুবিদিত।
ফলে তারকেশ্বরের সঙ্গে পিয়াসাড়ার জমিদাররা যুক্ত হলেও বর্ধমান রাজের তাতে আপত্তি থাকার কথা ছিল না। তাই একদিকে মোহান্তর সমর্থন, আর অন্যদিকে বর্ধমান রাজের প্রশ্রয়, এই দুই-এ মিলে পিয়াসাড়ার জমিদারদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকল।
১৮৭৩।
তারকেশ্বরের মোহান্ত তখন মাধবচন্দ্র গিরি।
শোনা যায়, তারকেশ্বরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের এলোকেশী নামক এক বিবাহিতা রমণীর সতীত্বনাশের অভিযোগে এই মোহান্ত তখন অভিযুক্ত হন।[৪]
গ্রামের বয়স্ক লোকের অভিমত, কোনও এক কারণে এইসময় নাকি পিয়াসাড়ার জমিদাররা মোহান্তকে আশ্রয় দেন।
যদিও তাতে কোনওই লাভ হয়নি।
মোহান্ত ধরা পড়েন। এবং বিচারে তাঁর কারাবাস হয়।
যদিও তাতেও মোহান্ত-প্রীতি কিছুমাত্র কমেনি জমিদারদের।
সেটি আরও বেশি করে বোঝা যায়, যখন আরও এক মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরিকে নিয়েও নানান বিতর্ক ওঠে এবং পিয়াসাড়ার জমিদাররা আবারও মোহান্তর পক্ষ নেন!
 |
| সরকার বাড়ির চতুর্ভূজা দুর্গা |
কেউ কেউ মনে করেন, প্রজাদের প্রতি পিয়াসাড়ার জমিদাররা মোটেই যত্নবান ছিলেন না। তাই হয়তো’বা হুগলি জেলার ইতিহাসে এইরকম প্রতাপশালী জমিদার-বংশের ইতিহাস প্রায় গুরুত্বহীন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছেই অজানা হয়ে পড়েছে।
কিন্তু পিয়াসাড়া গ্রামের জমিদারদের সুবিশাল বাড়ি দেখলে আজও থমকে দাঁড়াতে হয়। উঁচু উঁচু থামগুলো আজও অতীতের ঔদ্ধত্য যেন প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করায়।
প্রশস্ত দালান। কড়ি-বরগার ছাদ। হাতি-গলা গেট। হাতি বাঁধার শিকল। সবটা জুড়ে এক অদৃশ্য টানে নিমেষে যেন মন চলে যায় সেই-ই অতীত দিনে।
দুর্গাপুজো আজও হয়। প্রতিমা এখানে চতুর্ভুজা। একচালার মধ্যেই বিরাজ করছেন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্ত্তিক। যদিও এই ‘চতুর্ভূজা’-র ব্যাখ্যা কী, এর সদুত্তর এ বাড়ির লোকেরাও জানেন না। তবে এ কথা সত্যি, শম্ভু-নিশুম্ভ বধের সময় দেবীর চতুর্ভুজা রূপ ছিল। যদিও দেবী-মূর্তির সঙ্গে এখানে কিন্তু মহিষাসুরই আছেন!
সরকার বাড়ির কুলদেবতা অবশ্য শান্তিনাথ শিব।
গাঁয়ে একটি কালীমন্দির আছে। আছে একটি ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দিরও।
চৈত্র মাসে শিবের গাজনের সময় এখানে মিলে-মিশে যান ধর্মরাজ ঠাকুর ও শিব। সরকার বাড়ির ঠাকুর দালানে মহাসমারোহে পালিত হয় নীলাবতীর বিয়ে (কে নীলাবতী জানতে, এই লেখার নীচে দেখুন)।
গাঁয়ের গাজন উৎসবকে মন দিয়ে লক্ষ করলে লৌকিক সংস্কৃতির এক বিচিত্র রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
এককালে এই গাঁয়ের মোড়লরা ছিলেন ধর্মরাজের ‘ভক্ত্যা’। যাকে বলে সন্ন্যাসী।
ধর্মরাজের গাজন এই গ্রামে তখন ধুমধাম করে হত। কিন্তু তারকেশ্বরের সঙ্গে সরকার বাড়ির ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধর্মরাজের গাজন পরিবর্তিত হয় শিবের গাজনে।
তা সত্ত্বেও তারকেশ্বরের মোহান্তরা শৈব-উপাসনার সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতির মিশ্রণের একটা সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ফলে এই অঞ্চলের গাজনে ধর্মঠাকুরের প্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত তো হয়ই নি, উল্টে নানান লোকাচারের মধ্যে ধর্মঠাকুর এখনও স্ব-মহিমাতেই রয়ে গিয়েছেন।
গাজনের ‘ডাক’-এ সেই সাড়া মেনে, পিয়াসাড়া গ্রামের সন্ন্যাসী আজও হাঁক পাড়েন, “ও বাবা ধর্মরাজের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব...”
জমিদারবাড়ির একটা অংশকে বলা হয় নতুন-বাড়ি।
পুরনো বাড়িতে দুর্গাপূজোর সাথে পাল্লা দিয়ে এ বাড়িতে একসময় বসন্তকালে আয়োজিত হত বাসন্তী-পূজা। তবে সেই পূজা আজ আর হয় না।
জমিদারদের সেই রমরমাও আজ আর নেই। সরকারদের বর্তমান বংশধররা গ্রামের আর পাঁচটা মানুষের মতোই ছোটবড় নানান পেশায় যুক্ত।
 |
| ভাঙন ধরা ইটের পাঁজরের গায়ে যেন হারানো অতীতের কান্না |
জমিদার বাড়ি নিয়ে এত কথা বলছি, তাতে মনে হতে পারে, পিয়াসাড়া গাঁ মানে বুঝি শুধুই এই সরকার বাড়ির ইতিহাস।
তা কিন্তু মোটেই না।
আন্দাজ দিতে সেই ইতিহাসে যাই।
মার্টিন রেলের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন । ছোট লাইনের ট্রেন। ব্রিটিশ যুগের।
তো তেমনই এক ট্রেনের যাতায়াত ছিল এই অঞ্চলে। সে পথে তখন চাঁপাডাঙার আগের স্টেশনের নাম ছিল এই পিয়াসাড়া।
ঠিক যে জায়গায় স্টেশনটি ছিল, সেই অঞ্চলের নাম আজও পিয়াসাড়া স্টেশন-বাজার। যদিও এই রেলপথ ১৯৭২ সাল থেকে বন্ধ। যদিও রেলপথটি আজও আছে পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে। পিয়াসাড়া হয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে অনুচ্চ বাঁধের মতো যে রাস্তা চলে গিয়েছে আঁটপুরের দিকে, এটিই সেই রেলপথ।
তবে একটি কথা না বললেই নয়, পিয়াসাড়া স্টেশন ও পিয়াসাড়া গ্রাম, এই দুটি আলাদা-আলাদা জায়গা। এই দুই জায়গার মধ্যেকার দূরত্ব প্রায় দেড় কিলোমিটার।
তো, এই যে গাঁয়ের ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও পরম্পরার কাহিনি, তাকে নিয়ে তেমন কোনও চর্চাই তেমন চোখে পড়ে না। বরং অল্পবিস্তর যাঁরাও বা চর্চা করেছেন, সেখানেও কিছু কিছু যেন অসঙ্গতি!
সুধীর কুমার মিত্রের ‘হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থটির কথা বলি। সেখানে আমরা দেখি, উনবিংশ শতকের একটি সময়ে, ম্যালেরিয়ার মহামারীর চেহারা নিচ্ছে। তাতে পিয়াসাড়া গ্রামের জমিদার বলাইদাস সরকার বাসুড়ি গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করছেন। তারিখ ১৮৬৯ সালের ১৫ জুলাই। [৫]
বর্তমানে এই চিকিৎসালয়ের চিহ্নমাত্র নেই।
সে তো অন্য প্রসঙ্গ।
ঘটনা হল, সরকারদের কুরচিনামায় এই ‘বলাইদাস’ নামটিই পাওয়া যায় না। তার বদলে ‘বাহিরদাস’। তা’হলে? ইতিহাসবিদ ভুল? নাকি সরকারি নথি? সন্দেহ থেকেই যায়।
পিয়াসাড়া আর যে তথ্য সুধীর কুমার মিত্র ওই গ্রন্থটিতেই পাওয়া যাচ্ছে, তা’ হল, বাংলা ১৩৫৮ সালে হুগলি জেলায় একটি আলু চাষের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় পিয়াসাড়া গ্রামের কালীপদ মণ্ডল বিশেষ স্থান লাভ করেন। তিনি এক একর জমিতে ২৬২ মণ আলু উৎপাদন করে।[৬]
এর বাইরে পিয়াসাড়া গ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না।
গাঁয়ের বৃদ্ধ মানুষজন যাঁরা আছেন তাঁদের স্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে এখনও এই গ্রামকে কেন্দ্র করে কত শত কাহিনি বা গল্প শুনতে পাওয়া যায় শুধু।
তাঁরা চলে গেলে একবারেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে একটি গাঁ, তার জনপদ, তার নানা সুখ-অসুখের কাহিনি।
অবশ্যি, এ জাতির তাতে কী বা আসে যায়!
 |
| ‘অভিযুক্ত’ মোহান্তকে নিয়ে লেখা, সূত্রঃ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, সুধীর কুমার মিত্র |
ছবিঃ প্রতিবেদক
পুনশ্চঃ নীলাবতীর বিয়ে নিয়ে কাহিনির সংখ্যা দুটি। একটি পৌরাণিক আর একটি মৌখিক। পৌরাণিক কাহিনি মতে, তারকাসুর বধের জন্য শিবের সন্তান হওয়া ছিল আবশ্যক। কিন্তু শিব সেইসময় গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে শিবকে বিয়েতে রাজি করাতে ভক্তরা না খেয়ে আছেন দীর্ঘদিন।
মর্ত্যের বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিবের বিয়ের পক্ষে প্রচার করছেন। কিন্তু তবুও শিব অনড়। অবশেষে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনেই নাকি শিব রাজি হয়েছিলেন এবং এই দিনেই নীল অর্থাৎ শিবের সাথে পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বলে এই অনুষ্ঠানকে বলে নীল-পার্বতী বা নীলাবতীর বিয়ে। শিবের বিয়ের খবরে আশ্বস্ত হয়ে ঐ দিন আজও শিব-সন্ন্যাসীরা ফল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।
অন্য কাহিনিটি জনশ্রুতিমূলক। সতীর দেহনাশের পর সতী নীলধ্বজ রাজার কন্যারূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। রাজা তাঁর নতুন নাম দেন নীলাবতী। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন অর্থাৎ নীল ষষ্ঠীর দিনে নীলাবতীর সাথে শিবের বিয়ে হয়েছিল বলে আজও বাংলার শিবভক্তরা ঐ দিনটিতে নীলাবতীর বিয়ে নামক উৎসব পালন করেন।
পিয়াসাড়ার সরকার বাড়ির কুলদেবতা শান্তিনাথ শিবের সাথে এই দিন ঘটরূপী পার্বতীর বিয়ে হয়। পুত্রবতী রমণীরা ঐ দিন উপবাস করেন এবং নীলের ঘরে বাতি জ্বেলে তবেই আহার করেন। এই ব্রত পালন করলে সন্তান দীর্ঘায়ু হয় বলে মায়েদের বিশ্বাস। নীল-ষষ্ঠীর ব্রত, নীলাবতীর বিয়ে, গাজন সব মিলিয়ে লোক সংস্কৃতির অনন্য উপাদান রয়েছে এই ছোট্ট গ্রামটিতে।
ঋণঃ
[৩] তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব, সতীশ গিরি মোহান্ত প্রণীত
[৪] হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দে’জ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, তারকেশ্বর
[৫] প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, হরিপাল, পৃষ্ঠা ৬৪৫
[৬] প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, প্রকৃতি পরিচয়, পৃষ্ঠা ১০৫
শেষ
১ম পর্ব পড়ার জন্য
আমাদের ব্লগে প্রকাশিত আরও লেখা










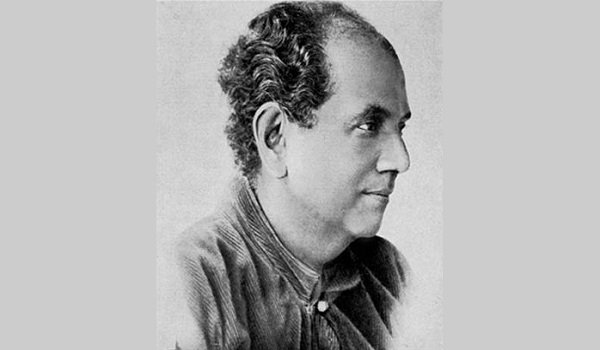

No comments:
Post a Comment