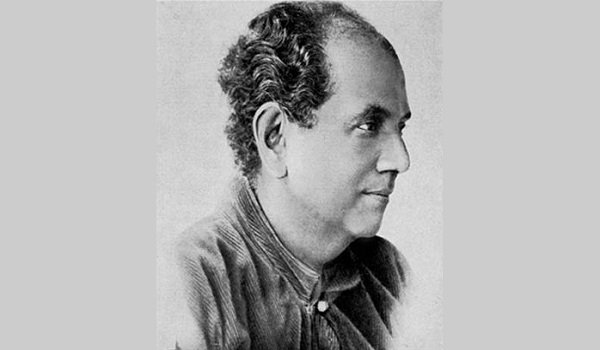চাঁদ সদাগর নাকি আদতে মুর্শিদাবাদের এক বণিক!
নবাবি আমল নয়, মুর্শিদাবাদের জন্ম রাজা শশাঙ্কেরও বহু আগে?
স্থানীয় লোককথা এমনই বলে!
যে কোনও ইতিহাসপ্রেমীর মাথায় চক্কর লাগিয়ে দেওয়ার জন্য এ দু’টি তথ্যই ঢের।
তার ওপর মুর্শিদাবাদে গোটা একটা যুগ কাটিয়ে এমন ধুঁয়াধার খবর কস্মিনকালেও পাইনি। ফলে পায়ের তলায় সরষে দানা চিড়বিড়িয়ে উঠল।
ফল? বাইকে চেপে সোজা ধাঁ।
গন্তব্য আমার আবাস মুর্শিদাবাদেরই কান্দি থেকে অল্প দূরে জজান!
 |
| সোমেশ্বর ঘোষের বংশধরদের রাজবাড়ি |
যাচ্ছি আর ভাবছি। যুদ্ধ, দেশপ্রেম, গুপ্তহত্যা, রাজনৈতিক চক্রান্ত, বেইমানি, আত্মত্যাগ। এবং অবশ্যই হাজারদুয়ারি। এর বাইরে বড়জোর পলাশীর যুদ্ধ।
এছাড়া তো মুর্শিদাবাদ ঘিরে কিচ্ছুটি মনে পড়ে না।
কিন্তু এ কী শুনলাম!!
নবাবি আমল নয়, খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক যে রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেটিও ছিল মুর্শিদাবাদেরই কর্ণসুবর্ণে!
চাঁদসওদাগর তো রূপকথা, অ্যাদ্দিন তাই জানতাম। কিন্তু এ তো বাস্তবের কথা বলে!
পৌঁছলাম অতীতের পাতায় হারিয়ে যাওয়া এক প্রাচীন রাঢ়ীয় গ্রামে।
জজান। ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে।
কান্দি শহরের থেকে ৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে।
আগে নাম ছিল জয়জান।
পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা গ্রামের মতোই জজানের চেহারা তেমন আলাদা নয়। শস্য-শ্যামলা। সুজলা-সুফলা। বিশ শতকের স্পর্শে আধুনিক অনেক বাড়ি থাকলেও অনেক মাটির বাড়িও চোখে পড়ল।
 |
| রাজবাড়িটির কিছু এখনও বর্তমান |
কায়স্থদের কুলগ্রন্থে থেকে জেনেছি, ৮০৪ শকাব্দ অর্থাৎ ৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থ বংশীয় সোমেশ্বর ঘোষ অন্যান্য চারজন কায়স্থের সঙ্গে মহারাজা আদি শূরের রাজসভায় এসেছিলেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে তারা সকলেই শ্ৰীশ্ৰী চিত্রগুপ্তদেবের অন্যতম পুত্ৰ শ্ৰীকর্ণের বংশধর বলে উল্লেখ। এখনও উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থরা ‘শ্ৰীকরণ’ নামে পরিচিত।
ইতিহাস বলে, ওই জয়যান গ্রামের চারপাশের বহু গ্ৰাম নিয়ে একটি সামন্ত রাজ্য গঠিত হয়। মহারাজ আদিত্যশূর বার্ষিক ১৫ শত টাকা কর নিৰ্দ্ধারণ করে সোমেশ্বর ঘোষকে এই সামন্ত রাজ্যের রাজা করে তোলেন।
সোমেশ্বর ঘোষ এখানে সোমেশ্বর শিব মন্দির ও সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তবে সেই প্রাচীন মন্দিরগুলি আজ আর নেই। তার বদলে রয়েছে তুলনায় নতুন মন্দির।
অবশ্য সোমেশ্বর ঘোষের বংশধরদের রাজবাড়িটির কিছু এখনও বর্তমান।
যদিও রাজবাড়িটি দেখে তার বয়স অনুমান করা সম্ভব না হলেও খুব প্রাচীন নয় বলেই মনে হল। এখন কোনও রাজা নেই। নেই পাইক-পেয়াদা, নেই রাজা-মন্ত্রী। রানীমহলে রানী-মাও নেই, নেই দাস-দাসী। নেই দরবার, প্রজাদের আনাগোনা। ঘোড়াশালে ঘোড়া উধাও, হাতিশালে নেই হাতি।
আছেটা কী?
জরাজীর্ণ মলিন বদন রাজবাড়িটি। চুরি হয়ে গেছে তার গরিমা। তার আভিজাত্য। জৌলুস। হারিয়েছে তার প্রতাপ। বদলে পালে পালে চামচিকের দল।
অথচ এক সময় সবই ছিল।
কারুকাজে ভরা বিশাল অট্টালিকা। শান বাঁধানো পুকুর ঘাট। রাজবাড়ির যত ঠাটবাট, সব।
 |
| সর্বমঙ্গলা মন্দির |
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি তল্লাটে। কাঁচা-পাকা রাস্তা বেয়ে। গাছগাছালিকে সঙ্গী করে।
সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির। গ্রামের আর এক পুরাতন ঐতিহ্য। স্থানীয়দের মুখে তার গল্প শুনলাম, রাজা সোম ঘোষ ‘স্বপ্নাদেশ’ পেয়ে এই মন্দিরের দেবী মূর্তিটি এক পুস্করিনী থেকে তুলে আনেন। তারপর প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। বর্তমান মন্দিরের গায়ে একটি প্রস্তর ফলক। সেখানে খোদাই করে লেখা— ৭০০ শকাব্দ, রামেশ্বর দত্ত, ৩৬০ বিঘা ভূমি দান।
রামেশ্বর দত্ত। এই মানুষটিরই কথা জেনে প্রথমেই তাক লেগে গিয়েছিল।
ওই অঞ্চলের পুরনো লোকেরা ওঁকে বলতেন চাঁদ সওদাগরের বংশধর।
অনুমান, রামেশ্বর দত্ত থাকতেন জজানের পশ্চিমে। বোদপুর গ্রামে। সেখানে একটি অঞ্চলের নাম রামদত্তের ডাঙা। জায়গাটি একসময় ছিল ‘গড়’ দিয়ে ঘেরা। তিনিও সেখানে সর্বমঙ্গলা মন্দির স্থাপন করেন। প্রথম যেখানে মন্দির গড়েন সেই স্থানটি আজও লোকে ডাকে ‘দেবস্থান’। রামেশ্বর দত্ত নিয়ে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না।
তবে সে কালে যে মানুষটি দেবীর পূজা নির্বাহের জন্য একসঙ্গে ৩৬০ বিঘা দান করেছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি ছিলেন অতি সঙ্গতি সম্পন্ন এক মানুষ।
দেবী সর্বমঙ্গলার সাবেক মন্দিরটি বয়সে অনেক নবীন হলেও তার ওপরের কারুকার্যগুলি যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও দেবী সর্বমঙ্গলা সাড়ম্বরে পূজিত হন। হয়্তো সেই প্রাচীন জাঁকজমক নেই।
জজান এককালে নদী ও বিলের কাছে থাকায় জলপথে বাণিজ্য করার প্রচুর সুযোগ ছিল। এই কারণে এই সমস্ত অঞ্চলে অনেক বণিক সেকালে বসবাস করতেন।
কান্দি-জজানের খুব কাছেই হিজলের বিল। যার সঙ্গেই চাঁদ সওদাগরের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে।
কান্দির এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিজলের নিম্নভূমি।
বর্ষাকালে সেখানে বানের জল জমে।
হিজল বিলের পাশ দিয়ে দ্বারকা আর ময়ুরাক্ষী নদী বয়ে যায়।
 |
| রাজবাড়িটির জরাজীর্ণ মলিন বদন |
শোনা যায়, মা মনসার অভিশাপে এই হিজলের বিলেই নাকি চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা ডুবেছিল। এখনও হিজলের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে মা মনসার প্রভাব বর্তমান।
মনে পড়ে যায়—
"মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ/ চম্পার কাছে/ এমনই হিজল-বট-তমালের নীল/ ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ/দেখিয়াছে।"
এখন হিজলে বাঁধ দিয়ে বহু জমি চাষযোগ্য করা হয়েছে। হিজলকে ঘিরে অনেক জমিদারি ছিল, তারা তাদের সুবিধামতো বাঁধ দিয়ে একটা সময় থেকে জমি ভরাট করে চাষ-আবাদ শুরু করেছে। ফলে বহু জমি ভরাট হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, অপরিকল্পিতভাবেই।
এক সময় হিজল কান্দি জেমো ও বাগডাঙ্গার জমিদারদের যৌথ খাজনা আদয়ের অন্তর্ভূত এলাকা ছিল।পরে গোটা অঞ্চলটি কয়েকটি জমিদারি মালিকানায় বিভক্ত হয়ে যায়।
নদীর জল যাতে প্লাবিত হতে না পারে, তাই নিজের নিজের এলাকা মাটির বাঁধ বা ঘের দিয়ে ঘিরে নেওয়ার ‘চল’ এখানে। তাই হিজলকে অনেকে 'ঘের'ও বলে।
যেমন— মাখনবাবুর ঘের , সোনাডাঙা ঘের, ষোলোভাগি ঘের ইত্যাদি।
চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে যে এই এলাকাগুলির সম্পর্ক আছে তার প্রমাণ মেলে পদ্মপুরাণে —
নবদূর্গা গোলহাট বামেতে রাখিয়া/চলিল সাধুর ডিঙা পাটন বহিয়া/দক্ষিন পাটনে যবে গেইলা সদাগর/শঙ্খ-মুক্তা-চুনি আইনা বোঝায় কৈলা ঘর।
এখনও সেই পাটনের বিল বহাল। সরকারি হিসাব বলে, এককালে জলা ছিল তিন হাজার বিঘার।
বিলের সাক্ষ্য মেলে কায়্স্থ কারিকাতেও। সেখানে লেখা, নবদূর্গা গোলহাটকে বাঁ দিকে রেখে চাঁদ সওদাগরের নৌকা পাটনের বিল দিয়ে যাতায়াত করত।
ঘুরতে ঘুরতে কেবলই বুঝতে পারছি, নবদূর্গা গোলহাট, কল্লা, জজান গ্রামগুলি চাঁদ সওদাগরের চিহ্ন কী ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে আজও!
কিন্তু চাঁদ সওদাগর কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন?
কেউ বলেন, তিনি আসলে পূর্ব বর্ধমান জেলার চম্পাই নগরীর বাসিন্দা। আবার কেউ কেউ বলেন বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর মনসাবিজয় (মনসামঙ্গল) কাব্যে চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথের বর্ণনায় চিৎপুর, বেতড়, কালীঘাট, চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদ্রিকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখি, সাতামুখি ও সাগরসঙ্গমের (সাগর দ্বীপ), ব্যান্ডেলের নাম উল্লেখ করেছেন। এমনকী বাংলাদেশ বা অসমের অনেক জায়গাতে আজও চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি বিজড়িত চিহ্ন বর্তমান।
তাহলে?
এ নিয়ে আজ অবধি কেউ কোনও গবেষণা করেননি।
আসলে প্রায় সবাই মনে করেন, চাঁদ সওদাগরের আসলে কোনও বাস্তবিক ভিত্তিই নেই!
একটি কল্পচরিত্র মাত্র!
অথচ জজানে এসে সে কথা ভাবাও যেন ধৃষ্টতা!
এমন তার আবেশ, এমন তার লতায়পাতায় মাখা লোককথা!
ফিরতি পথে উজান-হাওয়ায় জজান কিছুতেই মন ছাড়ে না।
বুকের কাছটা কেমন কেমন লাগে!
লোককথা, কল্পকাহিনি, ইতিহাস সব মিলিয়ে হারানো সড়কের খোঁজটা কী ভেবে মিলবে?
জানিনা!
ঋণঃ ১.বংশ-পরিচয় (অষ্টম খণ্ড) - জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ২. মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি – কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
আমাদের ব্লগে প্রকাশিত আরও লেখা